প্রথমে ঐসব বুনিয়াদী বিষয়ের আলোচনা হবে, যা কুরআন মাজিদ উপলব্ধিতে বিবেচনায় রাখা আবশ্যক:
উচ্চ আলংকারিক আরবি
প্রথম বিষয় হচ্ছে, কুরআন মাজিদ যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, তা উম্মুল কুরা [বা মক্কার] উচ্চ অলংকারের আরবি, যে ভাষায় জাহেলী যুগের কুরাইশ গোত্রের লোকেরা কথা বলতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহতাআলা তাঁর এ গ্রন্থের ভাষাকে অলংকার ও বাগ্মিতার এক চিরন্তন মুজেজা বানিয়েছেন, তথাপি নিজের উৎসমূলের দিক থেকে এটা সেই ভাষা, যাতে কথা বলেছেন স্রষ্টার প্রেরিত নবী এবং এটা ছিল তৎকালীন মক্কাবাসীর ভাষা।
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا۔
“আর (হে নবী) আমরা এ কুরআনকে আপনার ভাষায় এজন্য সহজ ও প্রাঞ্জল করেছি, যেন এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের সুসংবাদ দিতে পারেন এবং এর মাধ্যমে হঠকারী স্বভাবের লোকদের হুশিয়ার করতে পারেন।” (মারইয়াম ১৯:৯৭)
এ কারণে কুরআনের উপলব্ধি এ ভাষার সঠিক জ্ঞান, যথাযথ মেজাজ ও ভাষারূচির উপর নির্ভরশীল। কুরআনের গভীর উপলব্ধি এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আবশ্যক যে, ব্যক্তি এ ভাষার পাকাপোক্ত পণ্ডিত হবেন এবং নিজের মধ্যে আরবি ভাষারীতির এমন অন্তরঙ্গ মেজাজ ও রূচি তৈরি করবেন যে, অন্ততপক্ষে ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের উদ্দেশ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবেন না।
এ বাস্তবতা অধিক ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। উপরন্তু, এ ভাষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী এটা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এটা না হারিরি-মুতানাব্বি বা যামাখশারি-রাযি’র লেখা আরবি; আর না এটা বর্তমান মিশর-সিরিয়ার পত্র-পত্রিকা এবং এই এলাকাগুলোর সাহিত্যিক ও কবিদের কলমে লিখিত আরবি। এগুলো এক ধরনের আরবি বটে; তবে কুরআন যে আরবিতে নাযিল হয়েছে, যেটাকে আরবিয়ে মুআল্লা [উচ্চ আলংকারিক আরবি] বলা শ্রেয় — সেটার সাথে ভাষারীতি, গঠন, শব্দ ও বাগধারার দিক থেকে এ আরবির সাথে কম-বেশি যে পার্থক্য রয়েছে, তার উপমা: মির-গালিব এবং সাদি-খাইয়্যামে’র ভাষার সাথে আমাদের বর্তমান হিন্দুস্তান ও ইরানের সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত উর্দু ও ফারসির মধ্যকার পার্থক্য। বাস্তবতা হচ্ছে: [আধুনিক ও মধ্যযুগীয়] এ আরবি কুরআনের ভাষার প্রতি আপনার কোনো রূচি তৈরি করে না, বরং তা ঐ রূচি সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক। যিনি এই আরবিতে মনোনিবেশ করবেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কুরআনের উপলব্ধি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবেন।
ফলশ্রুতিতে কুরআনের ভাষার জন্য সর্বাগ্রে যে জিনিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তা স্বয়ং কুরআন মাজিদ। এ বাস্তবতা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, কুরআন যখন মক্কায় নাযিল হচ্ছিল, তখন এর ঐশ্বরিক মর্যাদা নিয়ে লম্বা একটা সময় বিতর্ক চললেও এর আরবি নিয়ে কেউ কখনো কোনো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। এজন্য বলা হয়: কুরআন কোনো অনারব লোকের কাজ হতে পারে না এবং এই দলীল দেয়া হয় যে, এটা নাযিল হয়েছে সর্বোত্তম প্রাঞ্জল আরবীতে। ভাষা ও সাহিত্য এবং অলংকার ও বাগ্মিতার এক মুজেজায় নিজেকে পরিণত করার পাশাপাশি কুরআন কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এটার অনুরূপ একটি সুরা বানানোর চ্যালেঞ্জ জানায়। এমনকি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে: এ কাজে সহায়তার জন্য তারা তাদের সাহিত্যিক, বক্তা, কবি, গণকসহ কেবল মানুষ নয়, বরং চাইলে জীন, শয়তান ও দেব-দেবীদের মধ্য থেকে যে কাউকে শামিল করতে পারবে।
কিন্তু এটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, আরবদের কেউ না পেরেছে কুরআনের আরবির শান-শওকতকে প্রত্যাখ্যান করতে, আর না কারো পক্ষে এর ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া সম্ভব হয়েছে।
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
“(এটা এ গ্রন্থের আহ্বান, তাই এ আহ্বানে সাড়া দাও), আর যা কিছু আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযিল করেছি, তার ব্যাপারে তোমরা যদি সন্দেহে থাকো (তাহলে যাও) এবং এর মতো একটি সুরা বানাও, আর (এ জন্যে) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যত সহযোগী আছে, তাদের ডাকো, যদি (তোমরা তোমাদের এ ধারণায়) সত্যবাদী হও।” (বাকারা, ২:২৩)
قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
“বলে দাও: আর যদি গোটা মানব ও জীনজাতি একত্র হয়ে বানাতে চায় এই কুরআনের অনুরূপ কিছু, তবে এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই তারা নিয়ে আসতে পারবে না — এমনকি তারা যদি পরস্পরের সহযোগী পর্যন্ত হয়।” (বনি ইসরাইল, ১৭:৮৮)
এখানেই শেষ নয়, উম্মুল কুরা [মক্কা]-’র ওলিদ ইবনে মুগিরার ন্যায় সাহিত্য সমালোচক পর্যন্ত কুরআনের ভাষা শুনে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠে:
واللّٰہ ، ما منکم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزہ ولا بقصیدہ مني ، ولا بأشعار الجن۔ واللّٰہ ، ما یشبہ الذي یقول شیءًا من ھذا۔ واللّٰہ ، إن لقولہ الذي یقولہ حلاوۃ و إن علیہ لطلاوۃ، و إنہ لمثمر أعلاہ، مغدق أسفلہ، وإنہ لیعلو ولا یعلٰی ، وإنہ لیحطم ما تحتہ۔
“আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্য থেকে কেউই আমার থেকে কবিতা সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে না — সেটা রণ-সংগীত, স্তুতি কাব্যই হোক, আর সেটা জীনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত মন্ত্রই হোক। আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তির কণ্ঠে যা ধ্বণিত হচ্ছে, তার কিছুই এগুলোর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। আল্লাহর কসম, এই লোকের বলা বাণীগুলো বেশ সুমিষ্ট ও বড়ই চমকপ্রদ। এর শাখা ফল-ফলাদিতে ভারী, আর শিকড় বেশ তরতাজা। এর বিজয় সুনিশ্চিত, পরাস্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অন্যদিকে এর চেয়ে নিম্নতর সবই এর দ্বারা ধূলিস্মাৎ হবে।” (আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)
সাবআ’ মুয়াল্লাকাতের অন্যতম কবি লাবিদ ঐ সময় জীবিত ছিলেন। লাবিদ এমনই উঁচু মাপের কবি ছিলেন যে, ফারাযদাকের মতো খ্যাতনামা কবিও তার একটি পংক্তির সামনে মাথা নত করেছিল। সেই লাবিদ কুরআনের ভাষা দ্বারা এতটাই বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, যখন সায়্যিদিনা উমর ফারুক তার কাছে কবিতা শোনার অনুরোধ জানান, তখন তিনি বলে উঠেন: [আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন বাকারা ও আলে-ইমরান, এরপর আমি আর কী কবিতা বলবো] — ‘ما کنت لأقول شعرًا بعد أن علمني اللّٰہ البقرۃ وآل عمران’।
এটা কেবল এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি নয়; বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে: গোটা আরবের অলংকার ও বাগ্মিতা পরাজয় বরণ করেছে কুরআনের ভাষার সামনে।
উপরন্তু, এটাও প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা যে, সামান্যতম পরিবর্তন ও একটি অক্ষরের হেরফের ছাড়াই ভাষা ও সাহিত্যের এই বিস্ময় আমাদের নিকট একেবারে আক্ষরিকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, এই বাস্তবতা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহর জমিনে কুরআনই কেবল দ্বীনের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, বরং স্বীয় যুগের ভাষার ক্ষেত্রেও কুরআনের ফয়সালাই শেষ কথা এবং এটাই চূড়ান্ত দলীল।
কুরআন মাজিদের পর নবীর হাদিস ও সাহাবিদের আসারের ভাণ্ডারে এই ভাষা পাওয়া যায়। এতে সন্দেহ নেই যে, [হাদিস ও আসারের বৃহৎ অংশ] রেওয়ায়েত বিল মা’না হওয়ায় এই ভাণ্ডারের সামান্য অংশ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় নমুনা ও প্রমাণক হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য। তা সত্ত্বেও যতটুকু বাকি আছে, তা সাহিত্যিক রূচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য মূল্যবান রত্ন।
এ ভাষা আরব ও অনারবের মাঝে সবচেয়ে স্পষ্টভাষী নবী মুহাম্মদ ও সাহাবিগণের প্রাঞ্জল বাকরীতি; এবং শব্দ-বাগ্ধারা ও ভাষারীতি বর্ণনার দিক দিয়ে এটা ঐ ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। নবী (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ)-এর দুআ, উপমা ও সাহাবিগণের সাথে তার কথোপকথন সাধারণভাবে রেওয়ায়েত বিল লাফয তথা বর্ণনাকারী দ্বারা হুবহু শাব্দিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর এ কারণে কুরআনীয় ভাষার অধিক নমুনা এসব রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে, কুরআনের ভাষার শিক্ষার্থী যদি এই ভরা সমুদ্রজলে ডুব দেয়, তবে সে বহু মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে; এবং কুরআনের শব্দ ও অর্থের নানা জটিলতা নিরসনে এ ভাণ্ডার থেকে বিপুল সহায়তা লাভে সক্ষম হবে।
এরপর এ ভাষার সবচেয়ে বড় উৎস আরবি সাহিত্য। এটা ইমরুল কায়েস, যুহায়ের, আমর ইবনে কুলছুম, লাবিদ, নাবিগা, তারাফা, আনতারা, আ’শা ও হারিছ ইবনে হালিযার ন্যায় কবি এবং কুস ইবনে সায়িদার ন্যায় বক্তার ভাষা। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে যে, এ সাহিত্যের বড় অংশ কবিদের দিওয়ান তথা কাব্য সংকলনে এবং “আসমায়িয়াত”, “মুফাদ্দিলিয়াত”, “হামাসা”, “সাবআ’ মুয়াল্লাকাত” এবং জাহিয ও মুবাররাদ-এর মতো অন্যান্য সাহিত্যিকের লিখিত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান সময়ে জাহেলী কবিদের বহু দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে, যা পূর্বে প্রকাশ পায়নি। এতে সন্দেহ নেই যে, আরবি ভাষার অধিকাংশ শব্দ ভাণ্ডার ঐ ভাষাভাষীদের ইজমা ও তাওয়াতুরের মাধ্যমে [আমাদের পর্যন্ত] পৌঁছেছে এবং এ শব্দ ভাণ্ডারের প্রধান উৎস: “তাহযীব”, “আল-মুহকাম”, “আস-সিবাহ”, “আল-জামহুরা” ও “আন-নিহায়া”-সহ অন্যান্য গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। তথাপি এর সাথে এটাও বাস্তবতা যে, আরবি শব্দ ভাণ্ডারের যে অংশ এমন মুতাওয়াতির নয়, সে অংশের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রমাণিক দলীলও আরবি সাহিত্য। এর মাঝে যদি কোনো জিনিসের সংযোজনও ঘটে, তবে ঠিক যেভাবে হাদিসের সমালোচক পণ্ডিতগণ বিশুদ্ধ ও দুর্বল বর্ণনার মাঝে পার্থক্য করতে পারেন, সেভাবে বর্ণনাসূত্র ও মূলপাঠের সুস্পষ্ট মানদণ্ডের আলোকে ভাষা সমালোচকগণ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জিনিস একে অপর থেকে আলাদা করতে সক্ষম। ফলশ্রুতিতে, শব্দ ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ সর্বদা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের পর এই সাহিত্যের উপর নির্ভর করা যায়; এবং বর্ণনা পরম্পরার শুদ্ধতা ও রেওয়ায়েত বিল লাফয দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় এ সাহিত্য নমুনা ও প্রমাণকের মর্যাদা রাখে।
[চলবে]
বই: মিজান
লেখক: জাভেদ আহমেদ গামিদি
অনুবাদক: ইমদাদ হোসেন
লেখাটি ত্রৈমাসিক আল-ইশরাক বাংলা জুন ২০২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল
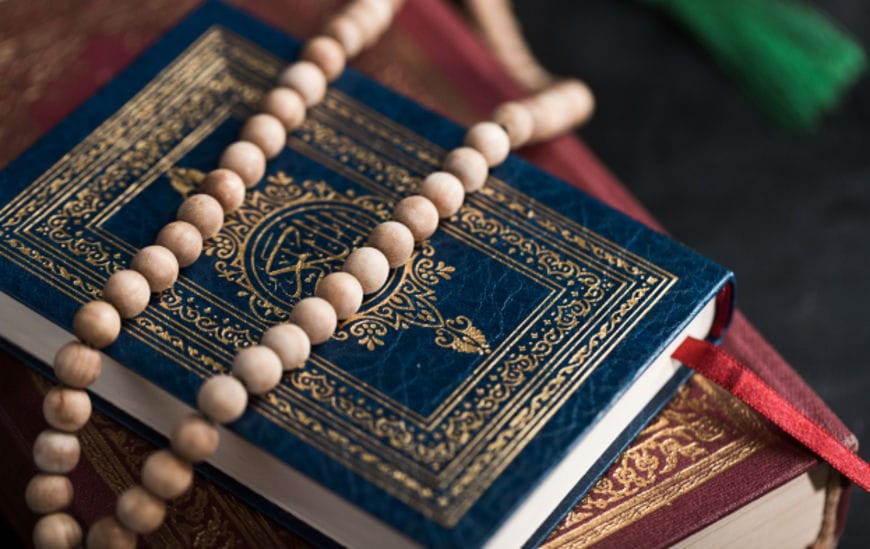
Leave a Reply